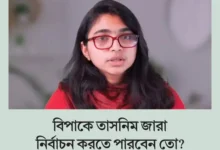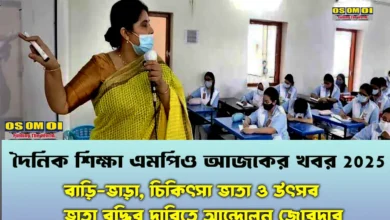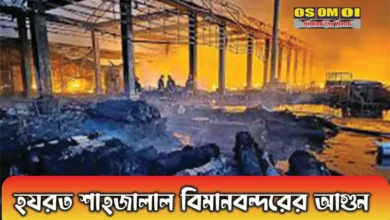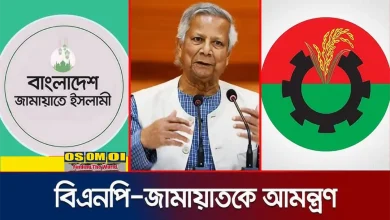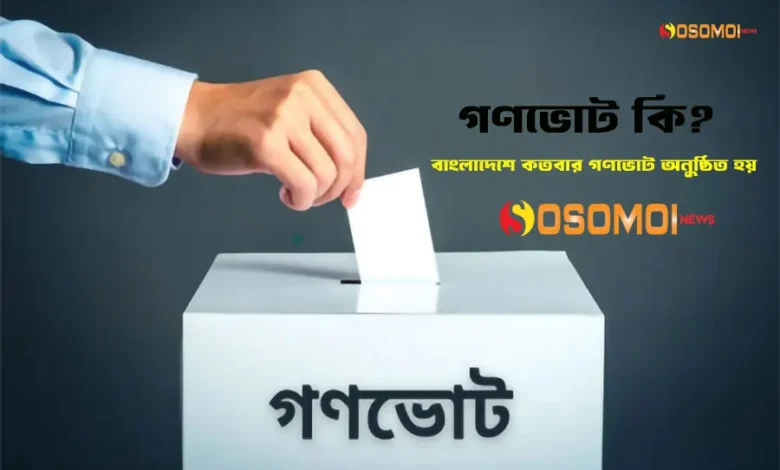
গণভোট কি
বাংলাদেশে কতবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়
গণভোট হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ জনগণের সরাসরি মতামত নেওয়া হয়।
সহজভাবে বললে — সরকার বা রাষ্ট্র কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায়, যেমন নতুন সংবিধান, বড় কোনো আইন, বা রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন। তখন সেই সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে ভোটের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয় — “আপনি রাজি কি না?”
উদাহরণ হিসেবে ধরো:
যদি কোনো দেশ চায় সংসদীয় পদ্ধতি থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতিতে যেতে, তাহলে সরকার সেটা একা ঠিক না করে জনগণের কাছে ভোট চাইতে পারে। জনগণ তখন “হ্যাঁ” বা “না” ভোট দেয়। ফলাফলই বলে দেয় সিদ্ধান্তটি কার্যকর হবে কি না।
এটা সাধারণ নির্বাচনের মতো নয়, কারণ এখানে প্রার্থী বেছে নেওয়া হয় না — সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কোনো একটি প্রশ্নের পক্ষে বা বিপক্ষে।
সংক্ষেপে,
গণভোট = জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত।
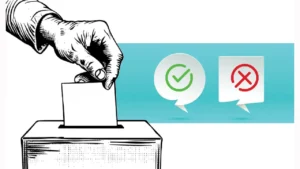

বাংলাদেশে কতবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়
বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মাত্র একবারই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এটা হয়েছিল ১৯৭৭ সালের ২১ মে, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে।
প্রেক্ষাপট:
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর দেশে একের পর এক সামরিক পরিবর্তন ঘটে।
শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে ছিলেন, কিন্তু তখন তার ক্ষমতার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।
এই বৈধতা “জনগণের সমর্থনের মাধ্যমে” প্রমাণ করার জন্যই তিনি গণভোটের উদ্যোগ নেন।
গণভোটের তারিখ:
২১ মে ১৯৭৭
প্রশ্নটি কী ছিল:
ভোটারদের সামনে একটি সরল প্রশ্ন রাখা হয়েছিল:
“আপনি কি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত জাতীয় কর্মসূচি ও নীতির প্রতি আস্থা রাখেন?”
ভোটারদের উত্তর দেওয়ার সুযোগ ছিল দুইভাবে:
-
হ্যাঁ (Yes)
-
না (No)
ফলাফল:
সরকারি হিসেবে,
-
মোট ভোটারদের প্রায় ৮৮% ভোট দিয়েছিল
-
এর মধ্যে ৯৮.৮৭% “হ্যাঁ” ভোট পড়ে
-
মাত্র ১.১৩% “না” ভোট
অর্থাৎ, ফলাফল অনুযায়ী, বিপুল সংখ্যক মানুষ জিয়াউর রহমানের পক্ষে ভোট দেয়।
তবে অনেক গবেষক ও ইতিহাসবিদ পরে বলেন — ভোটের আয়োজন, ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ প্রক্রিয়া নিয়ে তখন নানা বিতর্ক ছিল। বিরোধী দল ও অনেক পর্যবেক্ষক দাবি করেন, নির্বাচনটি পুরোপুরি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ছিল না।
এর পর আর কোনো গণভোট?
না, এরপর থেকে বাংলাদেশে আর কোনো গণভোট অনুষ্ঠিত হয়নি।
সংবিধানে গণভোটের বিধান থাকলেও (বিশেষ করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতি পরিবর্তনে), কোনো সরকারই পরবর্তীতে সেই পথ বেছে নেয়নি।
সংক্ষেপে বলা যায়:
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| মোট গণভোট সংখ্যা | ১ বার |
| তারিখ | ২১ মে ১৯৭৭ |
| রাষ্ট্রপতি | জিয়াউর রহমান |
| মূল উদ্দেশ্য | ক্ষমতার বৈধতা ও জনসমর্থন যাচাই |
| ফলাফল | ৯৮.৮৭% “হ্যাঁ” ভোট |
| বিতর্ক | ফলাফলের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন |
আরো পরুন
বিশ্বজয়ী হাফেজ সাইফুর রহমান ত্বকী ।বাংলাদেশ হারাল এক গর্বের সন্তান
Nadiya Akter Bristy Viral Video : একটা ভিডিও থেকে কত টাকা আয় করতেন যুগল দম্পত্তি
দৈনিক শিক্ষা এমপিও আজকের খবর 2025 :বাড়ি-ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন জোরদার
IMF প্রবাসীদের আয়ের ওপর কর বসাতে চায়? জানুন পুরো প্রস্তাব ও সরকারের প্রতিক্রিয়া
পি আর পদ্ধতি নির্বাচন কী। কিভাবে হয়, এবং কিভাবে নির্বাচিত হয়? (বাংলা বিশ্লেষণ)


বাংলাদেশে কতবার জরুরি অবস্থা জারি হয়
বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মোট পাঁচবার (৫ বার) জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে।
প্রতিটি ঘোষণার পেছনে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক হস্তক্ষেপ বা বড় জাতীয় সংকট কাজ করেছে।
১. প্রথম জরুরি অবস্থা — ১৯৭৪
তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪
কে জারি করেছিলেন: রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান
কারণ:
-
খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ
-
রাজনৈতিক অস্থিরতা
-
দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা
এই সময় সরকার গণবিক্ষোভ দমন এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।
২. দ্বিতীয় জরুরি অবস্থা — ১৯৭৫
তারিখ: ২৫ আগস্ট ১৯৭৫
কে জারি করেছিলেন: রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ
কারণ:
১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট ও সেনা অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে দেশকে “স্থিতিশীল” রাখার অজুহাতে এই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।
৩. তৃতীয় জরুরি অবস্থা — ১৯৮১
তারিখ: ৩০ মে ১৯৮১
কে জারি করেছিলেন: ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
কারণ:
রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রামে হত্যা করা হয়েছিল। তার পরই দেশজুড়ে অনিশ্চয়তা ও সেনা টানাপোড়েন তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।
৪. চতুর্থ জরুরি অবস্থা — ১৯৮৭
তারিখ: ২৭ নভেম্বর ১৯৮৭
কে জারি করেছিলেন: রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
কারণ:
বিরোধী দলগুলোর টানা আন্দোলন, হরতাল ও বিক্ষোভে সারাদেশে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এরশাদ সরকার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।
৫. পঞ্চম জরুরি অবস্থা — ২০০৭
তারিখ: ১১ জানুয়ারি ২০০৭
(জনপ্রিয়ভাবে “১/১১ জরুরি অবস্থা” নামে পরিচিত)
কে জারি করেছিলেন: রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ (তখন তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানও ছিলেন)
কারণ:
২০০৬ সালের শেষের দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন নিয়ে বড় রাজনৈতিক সংঘাত হয়।
বিএনপি ও আওয়ামী লীগ মুখোমুখি অবস্থানে যায়, দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।
শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।
এই জরুরি অবস্থা প্রায় দুই বছর স্থায়ী ছিল — ডিসেম্বর ২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে শেষ হয়।
সংক্ষেপে টেবিল আকারে:
| ক্রম | বছর | রাষ্ট্রপতি | প্রধান কারণ |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৯৭৪ | শেখ মুজিবুর রহমান | দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক সংকট |
| ২ | ১৯৭৫ | খন্দকার মোশতাক আহমেদ | বঙ্গবন্ধু হত্যার পর অস্থিতিশীলতা |
| ৩ | ১৯৮১ | বিচারপতি আবদুস সাত্তার | জিয়াউর রহমান হত্যার পর অস্থিরতা |
| ৪ | ১৯৮৭ | হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ | বিরোধী আন্দোলন দমন |
| ৫ | ২০০৭ | ইয়াজউদ্দিন আহমেদ | নির্বাচনসংকট ও রাজনৈতিক সহিংসতা |
সংক্ষেপে,
বাংলাদেশে ৫ বার জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে — ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৮৭ এবং ২০০৭ সালে।


বাংলাদেশে কতবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়
এটা বোঝা দরকার কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একসময় ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়।
সংক্ষেপে বললে,
বাংলাদেশে মোট তিনবার (৩ বার) তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে (সংবিধান অনুযায়ী)।
তবে এর আগে ১৯৯০ সালে একবার অসংবিধানিকভাবে “অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার” হয়েছিল।
অর্থাৎ, সব মিলিয়ে বলা যায় — মোট ৪ বার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে।
চল একে একে দেখি:
১. প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার (অসংবিধানিক)
সময়: ডিসেম্বর ১৯৯০ – মার্চ ১৯৯১
প্রধান উপদেষ্টা: বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ
পটভূমি:
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এক দশকের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পর তিনি পদত্যাগ করেন।
বিরোধী দলগুলোর সমঝোতায় বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে প্রধান করে একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।
এই সরকার ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করে।
এই সময়ই দেখা যায় তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি কতটা কার্যকর হতে পারে — পরে এর ধারণাটিই সংবিধানে যুক্ত হয়।
২. দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার (সংবিধানিকভাবে প্রথম)
সময়: মার্চ – জুন ১৯৯৬
প্রধান উপদেষ্টা: বিচারপতি হাবিবুর রহমান
পটভূমি:
১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন বিএনপি সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়, কিন্তু প্রায় সব বিরোধী দলই বর্জন করে।
দেশব্যাপী আন্দোলনের মুখে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় (১৩তম সংশোধনী)।
এরপর বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় এবং ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (জুন ১৯৯৬) আয়োজন করে।
৩. তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
সময়: জুলাই – অক্টোবর ২০০১
প্রধান উপদেষ্টা: বিচারপতি লতিফুর রহমান
পটভূমি:
আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ শেষে সংবিধান অনুযায়ী এই সরকার গঠিত হয়।
এটি ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (অক্টোবর ২০০১) পরিচালনা করে, যেখানে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট জয়ী হয়।
৪. চতুর্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার (বিতর্কিত ও দীর্ঘতম)
সময়: জানুয়ারি ২০০৭ – জানুয়ারি ২০০৯
প্রধান উপদেষ্টা: প্রথমে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ (সংক্ষিপ্ত সময়), পরে ড. ফখরুদ্দিন আহমদ
পটভূমি:
২০০৬ সালের শেষ দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়।
বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দুই দলই মুখোমুখি অবস্থানে যায়, দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।
১১ জানুয়ারি ২০০৭ (যা “১/১১” নামে পরিচিত) সেনাবাহিনীর সহায়তায় ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।
এটি প্রায় দুই বছর ক্ষমতায় থেকে ২০০৮ সালের নির্বাচনের আয়োজন করে।
এরপর কী হলো?
২০১১ সালে ১৫তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।
এখন থেকে নির্বাচন হয় ক্ষমতাসীন দলের অধীন, যদিও বিষয়টি এখনো রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু।
সংক্ষেপে টেবিল আকারে:
| ক্রম | বছর | প্রধান উপদেষ্টা | বৈধতা | উল্লেখযোগ্য নির্বাচন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯৯০–১৯৯১ | বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ | অসংবিধানিক (সমঝোতা ভিত্তিক) | পঞ্চম সংসদ নির্বাচন |
| ২ | ১৯৯৬ (মার্চ–জুন) | বিচারপতি হাবিবুর রহমান | সংবিধানিক | সপ্তম সংসদ নির্বাচন |
| ৩ | ২০০১ (জুলাই–অক্টোবর) | বিচারপতি লতিফুর রহমান | সংবিধানিক | অষ্টম সংসদ নির্বাচন |
| ৪ | ২০০৭–২০০৯ | ড. ফখরুদ্দিন আহমদ | সংবিধানিক (কিন্তু বিতর্কিত) | নবম সংসদ নির্বাচন |
সংক্ষেপে,
বাংলাদেশে মোট ৪ বার তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে,
এর মধ্যে ৩ বার সংবিধান অনুযায়ী এবং ১ বার রাজনৈতিক সমঝোতায় (১৯৯০)।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাস হয়
বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে,
যখন সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী (Thirteenth Amendment) পাস করা হয়।
এটা ছিল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বড় এক মোড়।
কেন এই আইন দরকার হলো?
১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের পর যে “অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার” হয়েছিল, সেটা ছিল রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে — সংবিধানে তখন এর কোনো ধারা ছিল না।
পরে ১৯৯১ ও ১৯৬ সালের শুরুতে দেখা যায়,
সরকার পরিবর্তনের সময় নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।
১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বিরোধী দলগুলো বর্জন করলে রাজনৈতিক সংকট চরমে ওঠে।
এই চাপের মুখে তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের মার্চে সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপন করে এবং পাস করে।
১৩তম সংবিধান সংশোধন বিল
পাসের তারিখ: ২৬ মার্চ ১৯৯৬
গেজেট প্রকাশ: ২৮ মার্চ ১৯৯৬
এর মাধ্যমে সংবিধানে নতুন অধ্যায় — “তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা” যুক্ত হয়,
বিশেষ করে ধারা ৫৮(খ) থেকে ৫৮(চ) পর্যন্ত।
কী ছিল এই আইনের মূল বিষয়:
১. সংসদের মেয়াদ শেষ হলে বা বিলুপ্ত হলে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে।
2. এই সরকার নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হবে।
3. প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।
4. তাদের কাজ হবে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা এবং নির্বাচন পরিচালনা করা।
5. সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন।
এরপর কী হলো:
এই ব্যবস্থায় তিনটি জাতীয় নির্বাচন হয় —
-
১৯৯৬,
-
২০০১,
-
২০০৮ (যদিও ২০০৭–০৮ সালের সরকার কিছুটা ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল)।
পরে ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ১৫তম সংবিধান সংশোধন পাস করে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়।
সংক্ষেপে:
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| আইন পাসের বছর | ১৯৯৬ |
| সংশোধন নম্বর | ১৩তম সংবিধান সংশোধনী |
| পাসের তারিখ | ২৬ মার্চ ১৯৯৬ |
| সরকার | বিএনপি সরকার (খালেদা জিয়া) |
| উদ্দেশ্য | নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন আয়োজন |
| বাতিল | ২০১১ সালে, ১৫তম সংশোধনের মাধ্যমে |
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন এক পদ্ধতি, যেখানে নির্বাচনের সময় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব হতো নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে।
এটার মূল উদ্দেশ্য ছিল খুব সোজা:
“নির্বাচন যেন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় — কোনো দলীয় সরকারের প্রভাব ছাড়া।
কেন এই ব্যবস্থা চালু হয়:
বাংলাদেশে বহু বছর ধরে অভিযোগ ছিল যে, ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন হলে সেটি সুষ্ঠু হয় না।
১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে তীব্র আন্দোলন হয় —
বিরোধী দলগুলো দাবি তোলে যে, নির্বাচন কেবল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হওয়া উচিত।
শেষ পর্যন্ত এই চাপের মুখে তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করে।
এই ব্যবস্থার কাঠামো:
১. সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর বা মেয়াদ শেষ হলে, রাষ্ট্রপতি একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন।
২. এর প্রধান হবেন সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি (যদি তিনি না থাকেন, তবে পরবর্তী বিচারপতি বা উপযুক্ত ব্যক্তি)।
৩. তাঁকে সহায়তা করবেন সর্বোচ্চ ১০ জন উপদেষ্টা, যারা সবাই অরাজনৈতিক ব্যক্তি হবেন।
৪. তাদের প্রধান কাজ হবে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করে সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা।
৫. এই সরকারের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৯০ দিন।
কখন কখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বাংলাদেশে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়:
-
১৯৯৬ (জুন) – বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে
-
২০০১ (অক্টোবর) – বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে
-
২০০৮ (ডিসেম্বর) – ড. ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে
এর আগে ১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের পরও বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়েছিল, যা এই ব্যবস্থার অনুপ্রেরণা দেয়।
কেন এই ব্যবস্থা বাতিল করা হয়:
২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ১৫তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়।
কারণ হিসেবে বলা হয় — সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, এই ব্যবস্থা সংবিধানবিরোধী।
তবে বিরোধী দলগুলো (বিশেষ করে বিএনপি) আজও দাবি করে,
তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।
সংক্ষেপে টেবিল আকারে:
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রবর্তন | ১৯৯৬ সালে (১৩তম সংশোধনী) |
| উদ্দেশ্য | নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজন |
| মেয়াদ | সর্বোচ্চ ৯০ দিন |
| প্রধান উপদেষ্টা | অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি |
| মোট সরকার সংখ্যা | ৪ (১৯৯০, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৭) |
| বাতিল | ২০১১ সালে (১৫তম সংশোধনী) |
| বর্তমান অবস্থা | বাতিল, এখন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় |
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল এমন এক সমঝোতার ফল, যেটা এক সময় দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল —
কিন্তু পরবর্তীতে সেটাই আবার বিতর্কের কেন্দ্রে চলে যায়।